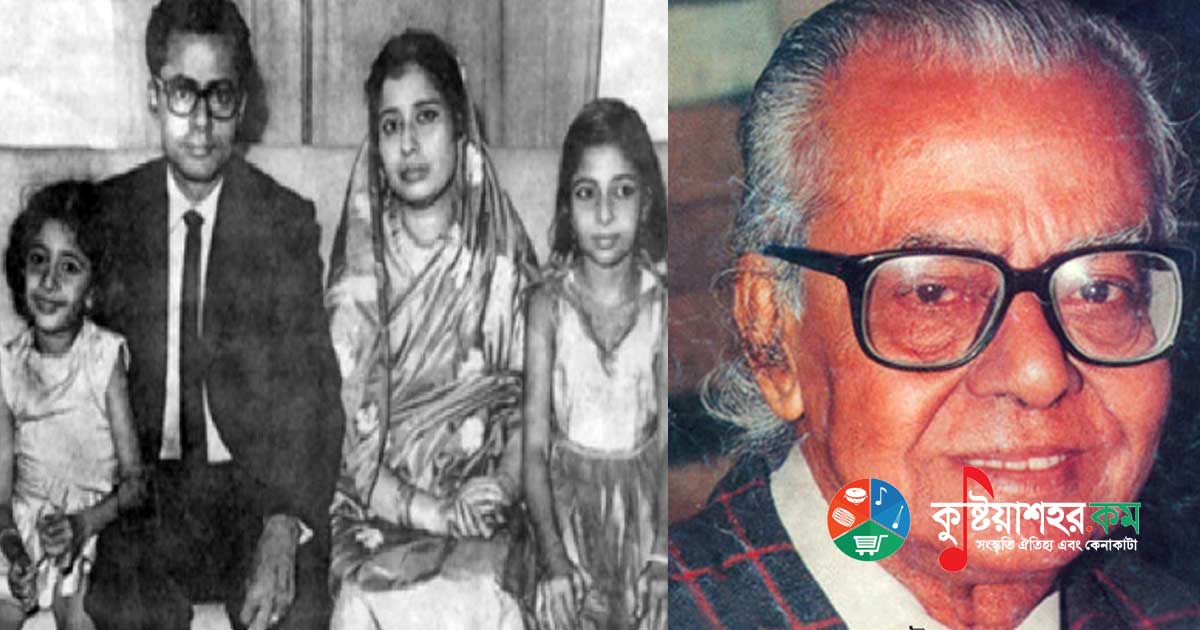নোয়াবেশ খাঁ:
পাঞ্জু শাহের সপ্তক ঊর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন নোয়াবেশ খাঁ। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় নি। এটুকুই মাত্র জানা গেছে যে, তিনি আফগানিস্তান থেকে এদেশে আসেন। খোন্দকার রফিউদ্দিন বলেন – “সম্রাট শাহজাহান যখন দিল্লির শাহী তখতে সমাসীন (১৬২৭-১৬৫৮), তখন পাঞ্জু শাহের সপ্তম ঊর্ধ্বতন পুরুষ মৌলভী মোহাম্মদ নোয়াবেশ খাঁ আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশে আসেন।” বঙ্গ সুবেদারের সুপারিশক্রমে দিল্লীর বাদশাহের ফরমান অনুসারে তিনি যশোর জেলার মহম্মদ শাহী পরগনার শৈলকূপা এলাকায় জমিদারি লাভ করেন।
নোয়াবেশ খাঁর পারিবারিক জীবন কাহিনী ও জমিদারী পরিচালনা বিষয়ক তথ্যাদি অজ্ঞাত। তবে তাঁর জনকল্যাণমূলক কিছু কাজের বিবরণ মিলেছে। এ সবের মধ্যে রাস্তা নির্মাণ, দীঘি খনন, মক্তব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
স্মরণ করা যেতে পারে, শৈলকূপা অঞ্চলে নোয়াবেশ খাঁ আসলে “নোয়াযেশ” খাঁ নামে পরিচিত। ঐ অঞ্চলের লোকসাহিত্য সংগ্রাহকগন মনে করেন, এই নোয়াযেশ খাঁ এবং গোলে বকালী পুঁথি রচয়িতা নোয়াযেশ খাঁ অভিন্ন ব্যাক্তি। আসলে বিষয়টি তা নয়। জমিদার নোয়াবেশ খাঁ বা নোয়াযেশ খাঁ এবং পুঁথি সাহিত্যের কবি নোয়াযেশ খাঁ ভিন্ন ব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি নোয়াযেশ খাঁ (১৬৩৮-১৭৬৫) চট্রগ্রাম জেলার সাতকানিয়ার অন্তর্গত সুখছড়ি গ্রামের অধিবাসী বলে উল্লেখিত হয়েছেন। অন্যদিকে নোয়াযেশ খাঁ ছিলেন আফগানিস্তান থেকে আগত শৈলকূপার জমিদার, যদিও কালের দিক থেকে উভয়ে সমসাময়িক।
দুদ্দু খাঁঃ
নোয়াবেশ খাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন দুদ্দু খাঁ। দুদমল্লিক খাঁ ছিল তাঁর আসল নাম। তাঁকে সচরাচর “দুদ্দু” নামে ডাকা হতো। পাঞ্জু শাহ্ তাঁর আত্ন-পরিচয়ে এই সংক্ষিপ্ত নামটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর ভাষায়—“নোয়াবেশ খাঁ বেটা দুদ্দু নাম তাঁর।” এ থেকে দুদ্দুর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, যদিও তাঁর সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অপ্রতুল।
দুদ্দুর মাতাপিতা আফগান হলেও তাঁর জন্ম হয় বাংলাদেশে। এদেশের আবহাওয়া, খাদ্য ও সমাজ-পরিবেশ তাঁর উপর এদেশীয় প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে তিনি খাঁটি বাঙ্গালীরূপে গড়ে উঠেন। বাল্যকালে পারিবারিক মক্তবে তিনি পড়াশোনা করেন। অভিজাত মুসলিম পরিবারে তখন আরবী-ফারসী অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। তবে অন্দর-মহলে ফারসী-উর্দু ব্যাবহার হলেও বাইরে বাংলা ভাষার কথা বলা হত। কারণ বাংলা ছিল সর্বসাধারণের ভাষা।
জমিদারী পরিচালনার সাথে সাথে দুদ্দু খাঁ ইসলামের মর্মবাণী প্রচার করতেন। পিতা বর্তমান থাকতেই তিনি জমিদারী তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বুঝে নেন। পিতার উপদেশ অনুযায়ী প্রজার সুখ-শান্তি বিধানের প্রতিও তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বাংলার তৎকালীন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ (১৭০৫-১৭২৭) দুদ্দু খাঁর জমিদারী বজায় রাখার সপক্ষে সমর্থন দান করেন বলেও জানা যায়।
এলেচ খাঁঃ
দুদ্দু খাঁর পুত্র-কন্যাদের মধ্যে এলেচ খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘এলেচ’ শব্দটি ‘ইলিয়াস’ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। পাঞ্জু শাহ্ তাঁর বনশ-বিবরণে ‘এলেচ’ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। ‘এলেচ খাঁ তাঁর বেটা’ বলে কবি যে উক্তি করেছেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
যথারীতি শিক্ষা গ্রহনের পর এলেচ খাঁ জমিদারী শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে খোন্দকার রফিউদ্দিন বলেন – ‘এলেচ খাঁ অত্যন্ত পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এ নীতি অনুসরন করে তিনি জমিদার পরিচালনা করতেন।’ শৈলকূপা (বৃত্তিদেবী রাজনগর) অঞ্চলের গ্রাম্য কবি বানুমোল্লা তাঁর একটি শায়েরীতে এলেচ খাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন –
তাঁর বেড়ে দাপট তাঁর।
বানু মোল্লা ভয়ে মলো,
ছাগল-বাঘে মিতে হলো।।’
উক্ত বানুমোল্লার শায়েরীতে অনেক প্রাচিন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এখানে উদ্ধ্রত শায়েরীটি তারই নমুনা। এলেচ খাঁ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তবে জমিদার হিসেবে তিনি ঐ অঞ্চলের অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর শাসন কালও বেশ দীর্ঘ ছিল এ সব তথ্য জানা গেছে।
আফজাল খাঁঃ
এলেচ খাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর পুত্র আফজাল খাঁ শৈলকূপার জমিদার হন। আফজাল খাঁ ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক। তাঁর সময়ে জমিদারীর আকার-আয়তন বৃদ্ধি পায়। শৈলকূপার পার্শ্ববর্তী কবীরপুর এবং অন্যদিকে হরিহারা পযন্ত সব গ্রাম এ জমিদারীর অন্তভুক্ত হয়। আফজাল খাঁ ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাদরদী জমিদার ছিলেন। গরীব প্রজারা তাঁর জমিদারীতে বিনা খাজনায় বাস করত এবং দুঃস্থ লোকেরা তাঁর কাছে আর্থিক সাহায্য পেত। তিনি শৈলকূপায় ‘পাঠান দীঘি’ নামে একটি বিরাট জলাশয় খনন করান। আজও এ দীঘি তাঁর সৃতি বহন করছে।
হরিহারা গ্রামে নতুন জমিদার ভবন নির্মাণ করে আফজাল খাঁ একটি বিস্ময়কর কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। জমিদার তত্ত্বাবধানের সুবিধার্থে তিনি বছরের ছ’মাস হরিহারা জমিদার ভবনে থাকতেন।
আফজাল খাঁ সম্পর্কে শৈলকূপা অঞ্চলে বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তিনি কখনও কবি, কখনও বীর বলে কথিত হয়েছেন। অনেকে আফজাল আলী নামক মধ্যযুগের এক কবিকে তাঁর সাথে এক করে দেখিয়েছেন। আসলে ব্যাপার তা নয়। কবি আফজাল আলী একজন পদকর্তা। চট্রগ্রামের সাতকানিয়া নিবাসী ভংগু ফকির ছিলেন তাঁর পিতা। খ্যাতনামা কবিদের সাথে তাঁর নামটিও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, কবি আফজাল আলী ও শৈলকূপার জমিদার আফজাল খাঁ ভিন্ন ব্যক্তি।
আবদুস সোহবান খোন্দকারঃ
জমিদার আফজাল খাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন আবদুস সোহবান খোন্দকার। পিতার পরলোকগমনের পর ইনিই শৈলকূপার জমিদার পদে অধিষ্ঠিত হন। উল্লেখ্য, আফজাল খাঁ পযন্ত এরা সবাই ‘খাঁ’ উপাধিধারী ছিলেন। কিন্তু আবদুস সোহবানের আমলে ঐ উপাধি পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন থেকে এঁদের নামের সঙ্গে ‘খোন্দকার’ উপাধী যুক্ত হয়। এটি কেমন করে হলো সে সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে।
‘খোন্দকার’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘অধ্যাপক’ বা শিক্ষক। ‘বাদশাহ’ অর্থেও ‘খোন্দকার’ শব্দটি ব্যাবহ্রত হত। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষক বুঝাতে ‘খোন্দকার’ শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মুসলিম সমাজে যারা পীর বা মুরশিদরূপে পরিচিত, তারাই ‘খোন্দকার’ নামে অভিহিত। এছাড়া বিয়ে পড়ানো, মসজিদে ইমামতী করা, ঈদের জামাত পরিচালনা, মৃত ব্যক্তির জানাজা সম্পাদন, তাবিজ-তুমার, ঝাড়ফুঁক প্রদান ইত্যাদিও খোন্দকারের কাজ। কিন্তু আবদুস সোহবান পীরগিরি করেই ‘খোন্দকার’ উপাধি লাভ করেন। পাঞ্জু শাহ্ের উক্তি থেকেও এ কথায় প্রমাণ মেলে। তিনি বলেনঃ-
তিনা হতে খোন্দকার দাদাজী আমার।।’
ঐ অঞ্চলে আবদুস সোবহান খোন্দকার ‘পীর-জমিদার’ হিসেবে কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে আছেন। শৈলকূপার অদুরে গাড়াগঞ্জ বাজারের কাছে ‘সোবহান খোলা’ নামে একটি বটবৃক্ষ তলে আজো এই পীরের নামে শিরনী হয়।
সোবহান খোন্দকারের ধর্মজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বহু ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শরীয়ত, তরিকত, হকিকত, মারিফাত ইত্যাদি চার স্তরেই শিষ্যগনকে তিনি শিক্ষা দিতেন। তাঁর সময়ে উক্ত জমিদারী এবং খোন্দকারী উভয়ই বজায় থাকে।
খাদেমালী খোন্দকারঃ
আবদুস সোবহান খোন্দকারের একমাত্র পুত্র খাদেমালী খোন্দকারই এ বংশের সর্বশেষ জমিদার। পিতার অবর্তমানে জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেন। তবে তাঁর মধ্যে ধর্মীয় চেতনা প্রবল থাকায় বৈষয়িক উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়।
জমিদারী তত্ত্ববধায়ক গোমস্তা এই সুযোগে তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে। তারই কারসাজীতে বহু সম্পত্তির সেস বাকী পড়ে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই অনেক জমি নিলামে উঠে। গোমস্তা তখন স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য আত্নীয়-স্বজনের নামে নিলাম খরিদ করে নেয়।
খাদেমালী খোন্দকারের জমিদারের জমিদারীর মোটা অংশ এভাবে গোমস্তা কৃতিত্বগত হয়ে পড়ে। তখন তা জানতে পারেন এবং গোমস্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন। বিপদ দেখে গোমস্তা দুর্বৃত্ত শ্রেণীর কিছু লোককে অর্থ দ্বারা বশীভূত করে জমিদারের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করে। গোপনে এ সংবাদ পেয়ে জমিদার খাদেমালী তখন সপরিবারে রাতের আঁধারে ঘরবাড়ী ছেড়ে শৈলকূপার পার্শ্ববর্তী হরিণাকুণ্ডু উপজেলার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামে চলে যান।
হরিশপুর নিবাসী ‘পরাণ কাজী’ ছিলেন খাদেমালী খোন্দকারের বড় জামাই। এই সুত্রে হরিশপুরে তাঁর যাতায়াত ছিল। এ গ্রামের আর একজন জোতদার ফকির মামুদ বিশ্বাসের সাথেও ঐ সময় তাঁর যথেষ্ট হ্রদ্যতা জন্মে। চরম বিপদের দিনে আত্নীয় নয়, বন্ধুর সহায়তাই তিনি কামনা করেন। উক্ত ফকির মামুদ বিশ্বাস তাঁকে পরম আদরে জায়গা দেন এবং হরিশপুরের পশ্চিমে বাটিকামারা বিলধারে ঘরবাড়ি করে দেন। জমিদার খাদেমালী খোন্দকার সেই থেকে হরিশপুরের স্থায়ী বাসিন্দা বলে গন্য হন। তাঁর পরিত্যক্ত ভু-সম্পত্তি এবং জমিদার গৃহ গোমস্তা কর্তৃক অধিকৃত হয়।
দারিদ্র্যের মধ্যেই খাদেমালী খোন্দকারের বাকী জীবন কাটে। মসজিদের ইমাম, সমাজের মোল্লা এবং ইসলাম প্রচারক হিসেবে তাঁর আত্নবিকাশ বেশ একটু বিস্ময়কর। বিশাল ভু-সম্পত্তি হারানোর কোন ক্ষোভ তাঁর মধ্যে দেখা দেয়নি। বরং ত্যাগের মহান শক্তিতে তিনি ছিলেন অটল। জীবনের শেষ দিন পযন্ত নিষ্ঠার সাথে মানুষকে ধর্মের কোথাই শুনিয়ে গেছেন তিনি।
১২৮৫ বঙ্গাব্দের (১৮৭৮ খ্রীঃ) ২০ শে ভাদ্র মঙ্গলবার এই মহান তাপস জমিদার ইহলোক ত্যাগ করেন। পাঞ্জু শাহের উক্তি থেকে এ তথ্য জানা যায়। পাঞ্জু শাহ্ বলেনঃ-
তাঁহার তারিখ আমি লিখিব হেথায়।।
বার শ’ পঁচাশি সাল বিশই ভাদ্রতে।
এন্তেকাল হন তিনি মঙ্গলবারেতে।।’
শেষ বিদায়ের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বছর। শান্তিপ্রিয় বিষয়ত্যাগী সাধক জমিদার খাদেমালী খোন্দকার চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন হরিশপুরের মাটিতে। তাঁর মাজার বাঁধানো হয়নি। কোন স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা এটি সনাক্তকরনের ব্যবস্থাও নেই। গ্রামবাসী ও তাঁর বংশধরগণ কবরের স্থানটি নির্দেশ করে থাকেন মাত্র।

 বাংলা
বাংলা  English
English